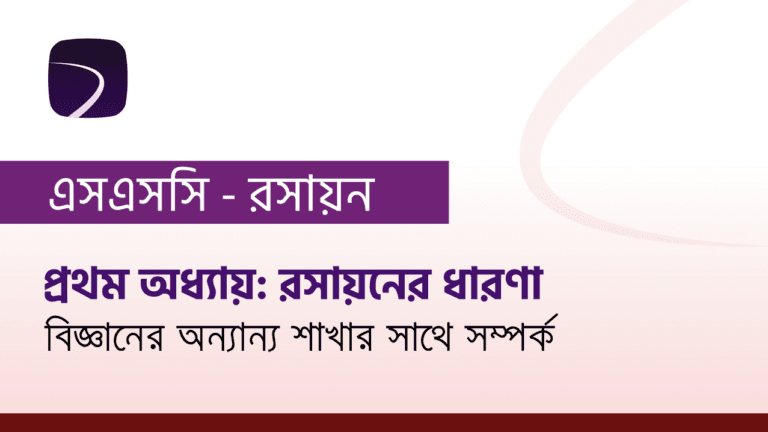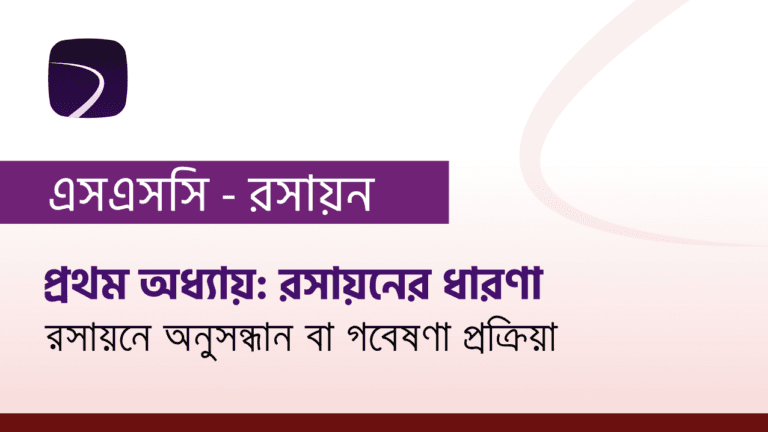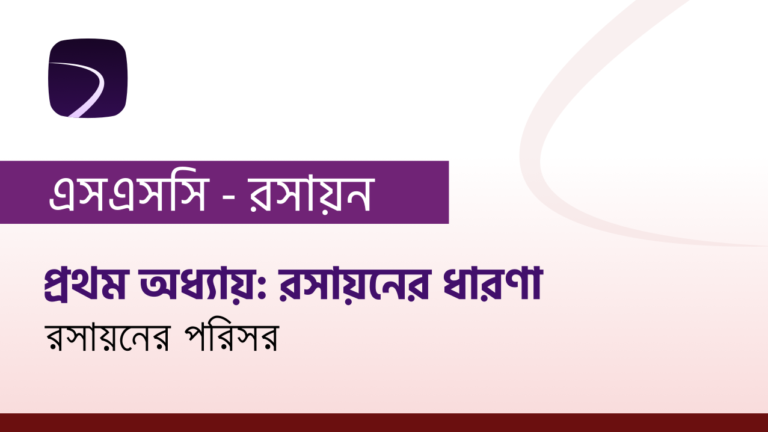- প্রথম অধ্যায় (রসায়নের ধারণা) – রসায়নের ক্রমবিকাশ
- প্রথম অধ্যায় (রসায়নের ধারণা) – রসায়ন পাঠের গুরুত্ব
- প্রথম অধ্যায় (রসায়নের ধারণা) – রসায়নের পরিসর
- প্রথম অধ্যায় (রসায়নের ধারণা) – বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সাথে সম্পর্ক
- প্রথম অধ্যায় (রসায়নের ধারণা) – রসায়নে গবেষণা প্রক্রিয়া
- প্রথম অধ্যায় (রসায়নের ধারণা) –পরীক্ষাগার ও রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারে সতর্কতা
- দ্বিতীয় অধ্যায় (পদার্থের অবস্থা) – কণার গতিতত্ত্ব ও পদার্থের ভৌত অবস্থা
- নবম অধ্যায় (এসিড-ক্ষারক সমতা) – এসিড, ক্ষারক ও ক্ষারের ধারণা
- নবম অধ্যায় (এসিড-ক্ষারক সমতা) – জলীয় দ্রবণে এসিড ও ক্ষারের আচরণ
- নবম অধ্যায় (এসিড-ক্ষারক সমতা) – প্রশমন বিক্রিয়া ও লবণ
- নবম অধ্যায় (এসিড-ক্ষারক সমতা) – লঘু এসিডের শনাক্তকারী ধর্মসমূহ ও পরীক্ষামূলক প্রমাণ
আসসালামু আলাইকুম। আমরা পরাবৃত্তের এসএসসি পদার্থবিজ্ঞান সিরিজের প্রথম পর্বে আমরা বিজ্ঞান ও এর প্রয়োগক্ষেত্র এবং শাখাবিন্যাস আলোচনা করেছি। রসায়ন সিরিজ শুরু করার আগে পরামর্শ থাকবে তা দেখে নিতে, কেননা ঠিক তার পর থেকে আমরা এখানে আলোচনা শুরু করছি।
পদার্থবিজ্ঞানের প্রেরণা যদি হয় প্রকৃতিকে গভীরভাবে জানা, তবে রসায়নচর্চার জন্য মানুষের প্রেরণা হলো কোন কিছুকে নতুন রূপ দেয়া বা নতুন কিছু তৈরি করা। আর তার জন্য জানতে হবে পদার্থের গঠন প্রকৃতি ও ধর্ম নিয়ে।
তাহলে রসায়ন কী? বিজ্ঞানের যে শাখায় পদার্থের গঠন, রাসায়নিক ধর্ম এবং পারস্পরিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া বা রূপান্তর নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে রসায়ন বলা হয়।
রসায়নের ক্রমবিকাশ
প্রাচীনতম উদাহরণ
প্রাতিষ্ঠানিকভাবে না হলেও জেনে না জেনে সুপ্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্নভাবে মানুষ রসায়নের ব্যবহার করেছে। আগুনের ব্যবহার করতে শেখা সম্ভবত নিয়ন্ত্রিতভাবে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটানোর সবচেয়ে প্রাচীন উদাহরণ হবে। প্রাচীন চিত্রকর্মের রঙ তৈরি ও ব্যবহারে সীমিত রাসায়নিক ধারণার প্রয়োগ দেখা যায়।
ব্রোঞ্জ যুগ
খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দের দিকে মানুষ কপার ও টিন ধাতু গলিয়ে দুটি তরলকে একসাথে মিশিয়ে তারপর পুনরায় ঠান্ডা করে সংকর ধাতুতে (alloy) পরিণত করে। কপার ও টিনের এই সংকর ধাতুর নাম ব্রোঞ্জ।
প্রকৃতিতে কপার ও টিন ধাতু পাওয়া গেলেও ব্রোঞ্জ পাওয়া যায় না- এটা মানবনির্মিত। ব্রোঞ্জ ধাতু কপারের থেকে মজবুত, অথচ একে গলানো ও বিভিন্ন আকৃতি দেয়া সহজ। কাজেই অস্ত্র ও বিভিন্ন সরঞ্জাম নির্মাণের জন্য ব্রোঞ্জ ধাতু সবার কাছে আদর্শ হয়ে উঠে।
মানবসভ্যতার অগ্রগতিতে ব্রোঞ্জের গুরুত্ব বোঝার জন্য এটুকু যথেষ্ট যে খ্রিস্টপূর্ব ৩৩০০ থেকে ১২০০ এই দুই সহস্রাধিক বছর সময়কালকে ব্রোঞ্জের বিস্তৃত ব্যবহারের কারণে ব্রোঞ্জ যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।
পদার্থের মৌলিক উপাদান ও পরমাণুর ধারণা
খ্রিস্টপূর্ব ৩৮০ অব্দের দিকে গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস পদার্থের অবিভাজ্য একক পরমাণুর ধারণা দেন। ডেমোক্রিটাসের পরমাণুর ধারণা ছিলো প্রত্যেক পদার্থকে অনবরত ভাঙতে থাকলে শেষ পর্যায়ে এমন এক ক্ষুদ্র কণা পাওয়া যাবে যাকে আর ভাঙা যাবে না। একে তিনি অ্যাটম নাম দেন যার অর্থ indivisible বা অবিভাজ্য।
কাছাকাছি সময়ে বৈশেষিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা কনাদ পরমাণুর ধারণা দেন। কনাদের পরমাণু ধারণা ছিলো এমন একটা পর্যায় যেখানে কোনরকম পরিমাপ সম্ভব না। তিনি দুটি ভরযুক্ত ও দুটি ভরহীন চার ধরণের পরমাণুর সমন্বয়ে সকল পদার্থের গঠনের কথা উল্লেখ করেন।
তবে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিলো অ্যারিস্টটলের মতবাদ। তিনি মনে করতেন সকল পদার্থ চারটি উপাদানে তৈরি- মাটি, পানি, বায়ু ও আগুন। এই উপাদানগুলোকে ক্লাসিকাল এলিমেন্টস বলা হয়।
এই মতবাদগুলো পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণিত ছিলো না। এধরণের মতবাদগুলো সাধারণত প্রাকৃতিক দর্শন হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়। তবে এই প্রাকৃতিক দর্শনের ধারা আধুনিক বিজ্ঞানের সূচনা করে দিয়েছে।
আলকেমি
আধুনিক রসায়নের পূর্বসূরী আলকেমি (alchemy)। পাঠ্যবই অনুযায়ী মধ্যযুগীয় আরবের রসায়ন চর্চাকে আলকেমি বলা হত। তবে এই সংজ্ঞা আলকেমির কিছুটা আংশিক চিত্র উপস্থাপন করে। রসায়নের সাথে আলকেমির প্রধানতম তফাৎ হলো রসায়ন বস্তুজগত নিয়ে সীমাবদ্ধ থাকলেও আলকেমি চর্চার সাথে বড় অংশে জড়িয়ে ছিলো আধ্যাত্মিকতা। আলকেমির মূল একটি উদ্দেশ্য ছিলো পরশ পাথর বা philosopher’s stone তৈরি। পরশ পাথর তৈরির এই প্রচেষ্টাকে বলা হত Magnus opum (মহৎ কর্ম)। মানুষের দেহ ও আত্মার বন্ধনকে মনে করা হত এই Magnus opum এর অংশ। ধারণা করা হত পরশ পাথর অন্য ধাতুকে সোনায় রূপান্তর করতে পারে এবং মানুষকে অমরত্ব দিতে পারে। বলা বাহুল্য, সে চেষ্টা সফল হয়নি।
ঐতিহাসিকভাবে আলকেমিচর্চার অন্তত তিনটি ধারা দেখা যায়, যাদের উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতিতে পার্থক্য ছিলো। চীনকে কেন্দ্র করে চৈনিক ধারা ও ভারতীয় উপমহাদেশে ভারতীয় ধারা এর মধ্যে দুটি। গ্রিসের দর্শনে উদ্বুদ্ধ আরেকটি ধারার চর্চা দেখা যায় তৎকালীন রোমান সাম্রাজ্যধীন মিশর ও বাইজেন্টাইনে। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতকে তার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় উসমানী ও আব্বাসীয় খেলাফতের অধীন মুসলিম সাম্রাজ্য। এই ধারার বিভিন্ন কাজ অনূদিত হয়ে ইউরোপে এসে পৌঁছায়।
আলকেমি মানুষকে পরশ পাথরের সন্ধান বা অমরত্ব দিতে না পারলেও বিভিন্ন পদার্থের রূপান্তর ও তার গবেষণার দুয়ার উন্মুক্ত করেছে। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের দিকে ধীরে ধীরে যা রূপ নিয়েছে আধুনিক রসায়নে।
আলকেমি শব্দটি আরবি আল-কিমিয়া থেকে এসেছে, যার মূল উৎস গ্রিক কিমি (Chemi বা Kimi), যেখান থেকে রসায়নের ইংরেজি Chemistry শব্দটি এসেছে।
জাবির ইবনে হাইয়ান
রসায়নের অগ্রগতিতে মধ্যযুগীয় আলকেমিস্ট জাবির ইবনে হাইয়ান বিশেষ ভূমিকা রাখেন। তিনি প্রথম গবেষণাগারে রসায়নের চর্চা শুরু করেন। তিনি তার পরীক্ষণ ও উপকরণের বর্ণনা যেভাবে করে গেছেন, তা তার আগে দেখা যায় না। অ্যারিস্টটলীয় মতবাদের চারটি উপাদান (মাটি, পানি, বায়ু এবং আগুন), এবং পঞ্চম উপাদান হিসেবে ইথারের ধারণা তার আগে ছিলো। তিনি এর সাথে আরো দুটি উপাদান- সালফার ও পারদকে মৌলিক উপাদান হিসেবে সংযোজন করেন। অনেক সময় জাবির ইবনে হাইয়ানকে রসায়নের জনক বলা হয়।
আধুনিক রসায়ন
আমরা বলেছি আলকেমির সাথে রসায়নের মূল পার্থক্য হলো প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অংশ হিসেবে রসায়ন কেবল প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার অধ্যয়ন ও প্রয়োগে সীমাবদ্ধ থাকে, যেখানে আলকেমির চর্চা অনেকাংশে আধ্যাত্মিকতা থেকে অবিচ্ছেদ্য ছিলো। ইউরোপে দ্বাদশ শতকের দিকে আলকেমির চর্চা শুরু হতে দেখা যায়। এরপর তা অনেক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে গেছে।
নিকোলাস ফ্লামেল, রজার বেকনসহ ইউরোপীয় অনেকে আলকেমি চর্চা করেছেন। বিজ্ঞানী নিউটন আলকেমিতে বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। এমনকি তিনি পদার্থবিদ্যা বা অপটিকস নিয়ে যত লিখেছেন, তার থেকে বেশি লিখেছেন আলকেমি নিয়ে।
যাইহোক, ইউরোপীয় এনলাইটেনমেন্টের (সপ্তদশ শতকের দিকের বিজ্ঞানের উত্থানসহ বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব) পর আধ্যাত্মিকতা, দর্শন ও অন্যান্য শাখা থেকে পৃথক হয়ে বিজ্ঞান শুধু বস্তুজগতের দিকে মনোযোগী হয়। আলকেমিচর্চার স্থান করে নেয় আধুনিক রসায়ন।
অ্যান্টনি ল্যাভয়েসিয়েকে বলা হয় আধুনিক রসায়নের জনক। রসায়ন গবেষণায় তার অবদানের তালিকা হবে বিস্তৃত। ল্যাভয়েসিয়ে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ভরের সংরক্ষণশীলতার নীতি উপস্থাপন করেন। তিনি ৩৩টি মৌলকে তালিকাবদ্ধ করেন। সর্বপ্রথম হিসেবে সচেতনভাবে পরিমাপের মাধ্যমে রাসায়নিক পরীক্ষণের ধারা শুরু করে তিনি পরিমাণগত রসায়নের অগ্রদূত হয়েছেন।
ল্যাভয়েশিয়ের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছিলো ট্র্যাজিকভাবে। ১৭৯৪ সালে ৫০ বছর বয়সে ফরাসী বিপ্লবের পর পূর্বের রাজতন্ত্রের সমর্থন, ট্যাক্স-দুর্নীতি ও বিপ্লবের বিরুদ্ধে অবস্থানের অভিযোগ দেখিয়ে ল্যাভয়েসিয়েকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়।
It took them only an instant to cut off this head, and one hundred years might not suffice to reproduce its like.
– ল্যাভয়েশিয়ের শিরশ্ছেদের পর তার সম্পর্কে জোসেফ লুইস ল্যাগরাঞ্জ