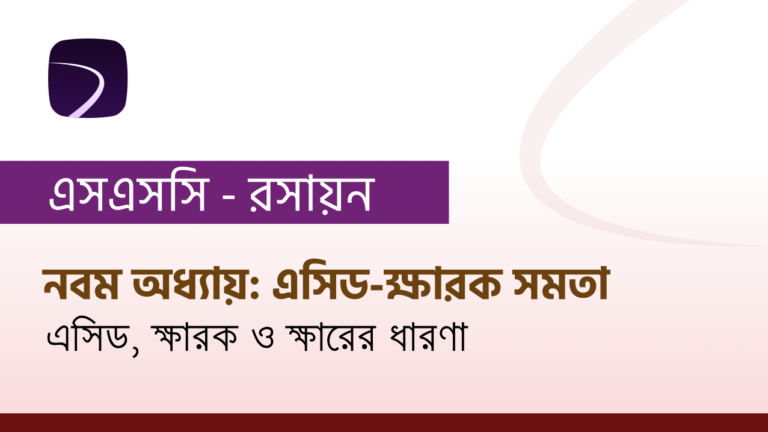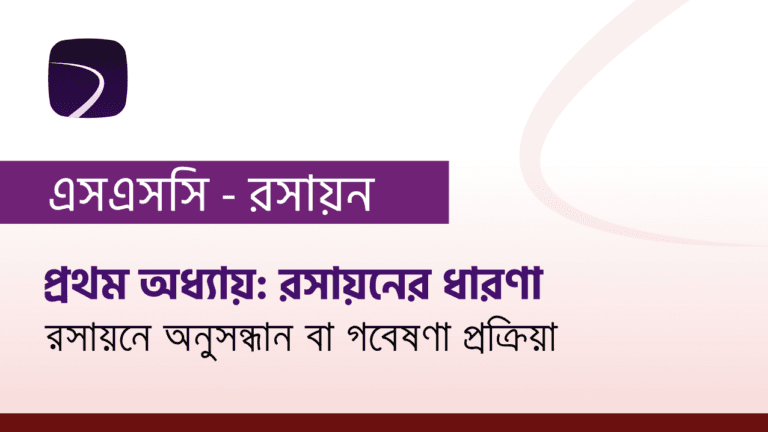- প্রথম অধ্যায় (রসায়নের ধারণা) – রসায়নের ক্রমবিকাশ
- প্রথম অধ্যায় (রসায়নের ধারণা) – রসায়ন পাঠের গুরুত্ব
- প্রথম অধ্যায় (রসায়নের ধারণা) – রসায়নের পরিসর
- প্রথম অধ্যায় (রসায়নের ধারণা) – বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সাথে সম্পর্ক
- প্রথম অধ্যায় (রসায়নের ধারণা) – রসায়নে গবেষণা প্রক্রিয়া
- প্রথম অধ্যায় (রসায়নের ধারণা) –পরীক্ষাগার ও রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারে সতর্কতা
- দ্বিতীয় অধ্যায় (পদার্থের অবস্থা) – কণার গতিতত্ত্ব ও পদার্থের ভৌত অবস্থা
- নবম অধ্যায় (এসিড-ক্ষারক সমতা) – এসিড, ক্ষারক ও ক্ষারের ধারণা
- নবম অধ্যায় (এসিড-ক্ষারক সমতা) – জলীয় দ্রবণে এসিড ও ক্ষারের আচরণ
- নবম অধ্যায় (এসিড-ক্ষারক সমতা) – প্রশমন বিক্রিয়া ও লবণ
- নবম অধ্যায় (এসিড-ক্ষারক সমতা) – লঘু এসিডের শনাক্তকারী ধর্মসমূহ ও পরীক্ষামূলক প্রমাণ
আমরা রসায়নের সংজ্ঞাতে রসায়নের আলোচনার তিনটি বিষয় বলেছি- পদার্থের গঠন, পদার্থের ধর্ম এবং পদার্থের পরিবর্তন। রসায়ন পাঠের গুরুত্ব তাহলে দাঁড়াচ্ছে পদার্থের গঠন, ধর্ম ও পরিবর্তন সম্পর্কে জানা কেন প্রয়োজন। চলো চিন্তা করে দেখি।
আমরা আলকেমির কথা যখন আগের অংশে বলেছি, মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে চেষ্টা করেছে অন্য ধাতুকে সোনায় পরিণত করার। যদি সেটা হয়, যেকোন কিছুকে যেকোন কিছুতে পরিণত করা যায়, তাহলে তো মজাই হত। কিন্তু হাজার বছরের সাধনায়ও তা সম্ভব হয়নি।
কিন্তু আমরা তো হরহামেশাই চারিদিকে পরিবর্তন দেখি, কামড় দেয়া আপেল অল্প সময়েই সাদা থেকে তামাটে হয়ে যায়, লোহায় মরিচা ধরে এবং কতরকম। তাহলে অন্য কিছুতে সোনাতেই বা পরিবর্তন করতে পারবো না কেন? আমাদের কি আরো হাজার বছর চেষ্টা করে যাওয়া উচিৎ? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা তখন দিতে পারবো যখন আমরা পদার্থ নিয়ে গভীরভাবে জানবো, তখন আমরা বুঝতে পারবো অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে লোহার অক্সাইড (মরিচা) তৈরি হওয়া আর এক মৌল থেকে অন্য মৌলে পরিবর্তন হওয়া এক ব্যাপার না।
কিন্তু লোহাকে যদি সোনায় পরিণত করতে নাও পারি, তারপরও এই যে বিভিন্ন পদার্থ ক্রিয়া-বিক্রিয়া করে, এগুলোকে কি আমরা নিজেদের কাজে লাগাতে পারবো না? পারলে কীভাবে? আবারো আমাদের দরকার হবে এই নিয়ে গভীর বৈজ্ঞানিক ধারণা।
এই যে নিত্যনতুন বিভিন্ন ওষুধের আবিষ্কার, কোন পদার্থের সাথে কোন পদার্থ মেশাতে হবে? কেমন নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ লাগবে তার জন্য? তা কীভাবে আমাদের দেহে প্রতিক্রিয়া করবে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তরের জন্য আবারো আমাদের যেতে হবে রসায়নের দিকে।
মানুষ বাড়ছে। আবাদি জমির জায়গায় গড়ে ওঠছে দালান। শিল্পায়নের কারণে কৃষি বা উৎপাদনমুখী কাজ ছেড়ে অন্যান্য দিকে যাচ্ছে অনেকে। তাহলে খাদ্যের চাহিদা কীভাবে পূরণ হবে? আমাদের অল্প জমিতে এখন বেশি উৎপাদন প্রয়োজন হবে। এজন্য উদ্ভিদকে যথেষ্ট পরিমাণ পুষ্টি উপাদান দিতে হবে, কীটপতঙ্গ থেকে মুক্ত রাখতে হবে। সার কিংবা কীটনাশক এবং বিভিন্ন ওষুধ- আবারো রসায়ন চলে আসবে এখানে।
বলা হয়, with great power comes great responsibility, অর্থাৎ বড় ক্ষমতা থাকলে থাকে বড় দায়িত্বও। রসায়ন সেরকম একটা বড় ক্ষমতা। কিন্তু মানুষ যে সবসময় খুব দায়িত্বশীল আচরণ করে, তা নয়। যেমন পরিবেশের নানারকম দূষণ, ফরমালিনসহ বিভিন্ন ক্ষতিকর পদার্থ দিয়ে সংরক্ষণ, কিংবা রাসায়নিক মারণাস্ত্রের ব্যবহার পর্যন্ত। আবার এর প্রতিকারেও কখনো কখনো সাহায্য করতে পারে রসায়ন।
রসায়ন যখন লাভ-ক্ষতির হিসাব করতে সাহায্য করতে পারে, তখন মানুষ হিসেবে দায়িত্বশীল হওয়ার দায়িত্ব আমাদের। বিশেষ করে জ্ঞান-বিজ্ঞানে আমরা যত শক্তিশালী হবো, এই দায়িত্বশীলতা তত বাড়বে। যেকারণে চারিদিকে যদি আমরা দেখি, বিজ্ঞান-শিল্প-প্রযুক্তির উন্নতির উপকারী দিক যত আছে, ক্ষতিকর দিক তাকে ছাড়িয়ে যাবে কিনা- তা নিয়ে বরং প্রশ্নের অবকাশ থেকে যায়। কিন্তু তাতে মানুষের জ্ঞানের দিকে অগ্রযাত্রা থেমে যাবে না আসলে। আর চারিদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখাও মানুষের বৈশিষ্ট্য নয়। তাই আমাদের জ্ঞানার্জন করতে হবে, এবং জ্ঞানকে উপকারী দিকে কাজে লাগাতে হলে ঠিক রাখতে হবে আমাদের উদ্দেশ্য ও দায়িত্ববোধের জায়গা।