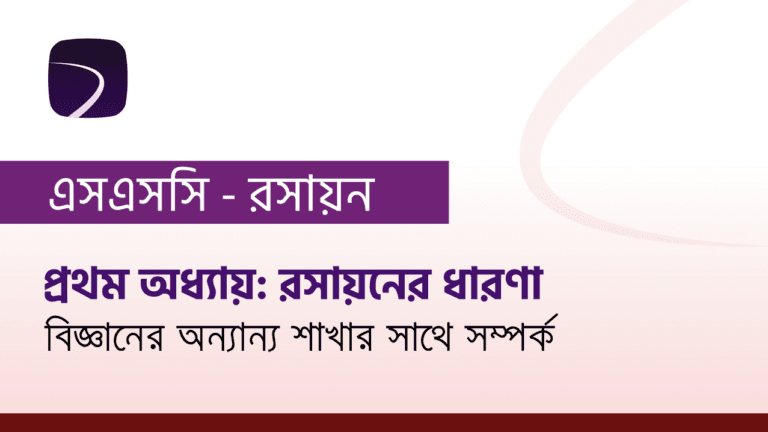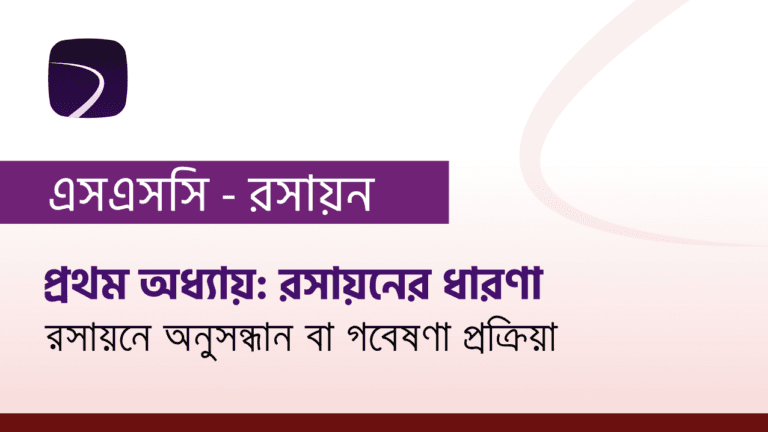- প্রথম অধ্যায় (রসায়নের ধারণা) – রসায়নের ক্রমবিকাশ
- প্রথম অধ্যায় (রসায়নের ধারণা) – রসায়ন পাঠের গুরুত্ব
- প্রথম অধ্যায় (রসায়নের ধারণা) – রসায়নের পরিসর
- প্রথম অধ্যায় (রসায়নের ধারণা) – বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সাথে সম্পর্ক
- প্রথম অধ্যায় (রসায়নের ধারণা) – রসায়নে গবেষণা প্রক্রিয়া
- প্রথম অধ্যায় (রসায়নের ধারণা) –পরীক্ষাগার ও রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারে সতর্কতা
- দ্বিতীয় অধ্যায় (পদার্থের অবস্থা) – কণার গতিতত্ত্ব ও পদার্থের ভৌত অবস্থা
- নবম অধ্যায় (এসিড-ক্ষারক সমতা) – এসিড, ক্ষারক ও ক্ষারের ধারণা
- নবম অধ্যায় (এসিড-ক্ষারক সমতা) – জলীয় দ্রবণে এসিড ও ক্ষারের আচরণ
- নবম অধ্যায় (এসিড-ক্ষারক সমতা) – প্রশমন বিক্রিয়া ও লবণ
- নবম অধ্যায় (এসিড-ক্ষারক সমতা) – লঘু এসিডের শনাক্তকারী ধর্মসমূহ ও পরীক্ষামূলক প্রমাণ
অধ্যায়ের নামে একটা মজার ব্যাপার আছে। এসিডের জন্য ইংরেজি শব্দ, ক্ষারকের জন্য বাংলা শব্দ নেয়া হয়েছে। এসিডের বাংলা অম্ল, ক্ষারকের ইংরেজি বেস (base)।
যাইহোক, এসিড ও ক্ষারক নিয়ে আলোচনার জন্য পুরো একটা অধ্যায় বরাদ্দ রাখা হয়েছে, কেন এরা এত গুরুত্বপূর্ণ? প্রথমত, জীবদেহে প্রতিনিয়ত হওয়া বিভিন্ন বিক্রিয়াসহ অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাথে এসিড ও ক্ষারক জড়িয়ে আছে। আমরা তার উদাহরণ এই অধ্যায়েই দেখবো। বিভিন্ন বিক্রিয়া সংগঠনে এসিডিক বা ক্ষারীয় পরিবেশ প্রভাব ফেলে। দ্বিতীয়ত, এসিড ও ক্ষারকের ধর্ম ও বিক্রিয়াকৌশল নিয়ে আমরা যা জানবো সে ধারণাকে আমরা সম্প্রসারণ করে আরো বড় পরিসরে প্রয়োগ করতে পারি। কাজেই এসিড ও ক্ষারকের ধারণা এবং বিক্রিয়াকৌশল রসায়নে বিশেষ গুরুত্ব পায়।
এসিড ও ক্ষারক: পাঠ্যবইয়ের সংজ্ঞা
এসিড: এসিড এক ধরনের গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক দ্রব্য যা পানিতে দ্রবীভূত করলে এসিডের অণু বিয়োজিত হয়ে (ভেঙে) হাইড্রোজেন আয়ন বা প্রোটন (H⁺) দান করে।
ক্ষারক: সাধারণত ধাতু বা ধাতুর মতো ক্রিয়াশীল যৌগমূলকের অক্সাইড এবং হাইড্রোক্সাইড যা এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে তাকে ক্ষারক বলে।
উদাহরণ ও ব্যাখ্যা
এসিড
HCl পানিতে দ্রবীভূত করলে নিম্নরূপে বিয়োজিত হয়-
HCl(aq) → H⁺(aq) + Cl⁻(aq)
এখানে aq দিয়ে aqueous বা জলীয় দ্রবণ বোঝাচ্ছে। যেখানে দ্রবীভূত অবস্থায় HCl বিয়োজিত হয়ে হাইড্রোজেন আয়ন দান করছে। কাজেই HCl একটি এসিড।
ক্ষারক
Na (সোডিয়াম) একটি ধাতু। Na এর শেষ কক্ষপথে একটি ইলেকট্রন আছে, যা ত্যাগ করে সে Na+ গঠন করতে পারে। Na+ এর অক্সাইড হলো Na2O (সোডিয়াম অক্সাইড) এবং হাইড্রোক্সাইড হলো NaOH (সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড)। আমরা যদি এসিডের সাথে এদের বিক্রিয়া দেখি-
Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O
NaOH + HCl → NaCl + H2O
এখানে ধাতুর অক্সাইড Na2O এবং হাইড্রোক্সাইড NaOH, এসিড HCl এর সাথে বিক্রিয়া করে NaCl (সোডিয়াম ক্লোরাইড) লবণ ও পানি উৎপন্ন করেছে। তাহলে আমাদের সংজ্ঞার সাথে মিলিয়ে আমরা Na2O ও NaOH কে ক্ষারক হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি।
অন্যদিকে NH4+ (অ্যামোনিয়াম আয়ন) একটি যৌগমূলক, যা রাসায়নিকভাবে ধাতব আয়ন, যেমন Na+ এর মত আচরণ করে। NH4+ এর হাইড্রোক্সাইড হলো NH4OH।
NH4OH + HCl → NH4Cl + H2O
তাহলে বলা যায় NH4OH হলো ধাতুর মত ক্রিয়াশীল যৌগমূলকের হাইড্রোক্সাইড, যা HCl এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে NH4Cl লবণ ও পানি উৎপন্ন করছে। তাহলে NH4OH একটি ক্ষারক।
প্রসঙ্গত, এসিড ও ক্ষার থেকে লবণ ও পানি তৈরি হওয়ার এই বিক্রিয়াকে প্রশমন বিক্রিয়া বলে।
ক্ষারের ধারণা
ক্ষারকের একটি প্রকারভেদ হলো ক্ষার (Alkali)। যেসমস্ত ক্ষার হাইড্রোক্সাইড যৌগ এবং পানিতে দ্রবণীয় তাদেরকে ক্ষার বলে।
আমরা ক্ষারকের সংজ্ঞাতে বলেছি ধাতু বা অনুরূপ আচরণকারী যৌগমূলকের অক্সাইড অথবা হাইড্রোক্সাইড যৌগ। তবে ক্ষারের মধ্যে শুধু হাইড্রোক্সাইড যৌগগুলো থাকবে। উদাহরণস্বরূপ, NaOH, NH4OH এরা ক্ষার। কিন্তু Na2O ক্ষারক হলেও ক্ষার না, যেহেতু এটা অক্সাইড যৌগ। আরেকটা শর্ত হলো পানিতে দ্রবণীয় হতে হবে, যেমন- Fe(OH)₃ (ফেরিক হাইড্রোক্সাইড) ধাতুর হাইড্রোক্সাইড যৌগ হলেও পানিতে দ্রবণীয়তা অত্যন্ত কম। এজন্য এটা ক্ষার হলেও ক্ষারক না।
সংযোজন ১: এসিড ও ক্ষারকের অন্যান্য সংজ্ঞা
পাঠ্যবইয়ে এসিডের সংজ্ঞা পানিতে বিয়োজনের দিক থেকে এবং ক্ষারকের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে প্রশমন বিক্রিয়াতে অংশ নেয়ার দিক থেকে। একারণে এসিড ও ক্ষারের সম্পর্ক বোঝা কিছুটা কঠিন হয়ে গেছে। তাই আমরা আরেকটু সুন্দরভাবে বোঝার জন্য অন্য সংজ্ঞাগুলো দেখবো।
১৮৮৪ সালে সুইডিশ বিজ্ঞানী আরহেনিয়াসের দেয়া সংজ্ঞা অনুসারে,
এসিড: যে রাসায়নিক দ্রব্য জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়ন (H⁺) এর ঘনত্ব বৃদ্ধি করে।
ক্ষারক: যে রাসায়নিক দ্রব্য জলীয় দ্রবণে হাইড্রোক্সাইড আয়ন (OH⁻) এর ঘনত্ব বৃদ্ধি করে।
আরহেনিয়াস সংজ্ঞা কেবলমাত্র জলীয় দ্রবণে আচরণ বিবেচনায় করে, আরো বড় পরিসরে এসিড ও ক্ষারকের ধারণা প্রয়োগের জন্য পরবর্তীতে ১৯২৩ সালে ব্রনস্টেড-লাউরী এভাবে সংজ্ঞা দিয়েছেন,
এসিড: যে রাসায়নিক দ্রব্য হাইড্রোজেন আয়ন (H⁺) দান করতে পারে।
ক্ষারক: যে রাসায়নিক দ্রব্য হাইড্রোজেন আয়ন (H⁺) গ্রহণ করতে পারে।
একই বছর আমেরিকান রসায়নবিদ লুইস আরো সম্প্রসারিত পরিসরে প্রয়োগের জন্য হাইড্রোজেন আয়নের পরিবর্তে ইলেকট্রন যুগল দান বা গ্রহণ করতে পারার ভিত্তিতে সংজ্ঞা দেন,
এসিড: যে রাসায়নিক দ্রব্য ইলেকট্রন যুগল গ্রহণ করতে পারে।
ক্ষারক: যে রাসায়নিক দ্রব্য ইলেকট্রন যুগল দান করতে পারে।
আরহেনিয়াস সংজ্ঞা প্রথম দিককার একটা সংজ্ঞা। তবে নবম-দশম শ্রেণিতে আমাদের আলোচনা মূলত জলীয় দ্রবণ বিবেচনা করে হবে, যেকারণে এই সংজ্ঞা সবচেয় প্রাসঙ্গিক। আরেকটু উচ্চতর পর্যায়ে বর্তমানে পরবর্তী সংজ্ঞাগুলো বেশি গুরুত্ব পায়। লুইস সংজ্ঞাতে এসিড হিসেবে বিবেচিত হয়, এমন অনেক রাসায়নিক দ্রব্য ব্রনস্টেড-লাউরী সংজ্ঞাতে এসিড বিবেচিত হয় না। এজন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্র অনুযায়ী দুটো সংজ্ঞা-ই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।
এই সংজ্ঞাগুলো নিয়ে আসা দুটো কারণে। প্রথমত, পাঠ্যবইয়ে এসিড ও ক্ষারকের মধ্যে সম্পর্ক বুঝতে অস্পষ্টতা দূর করা। দ্বিতীয়ত, এসিড ও ক্ষারকের ধারণা কীভাবে আরো সম্প্রসারিত পরিসরে প্রয়োগ করা হতে পারে তার একটি ধারণা দেয়া। প্রসঙ্গত, উচ্চ মাধ্যমিকে তিনটি সংজ্ঞা-ই আলোচিত হয়ে থাকে।
সংযোজন ২: ক্ষারক ও ক্ষারের মত এসিডের বিপরীতে কিছু নেই কেন?
ক্ষারকের বেলায় আমরা দ্রবণীয় এবং হাইড্রোক্সাইড মূলকযুক্ত ক্ষারকগুলোকে আলাদাভাবে ক্ষার হিসেবে চিহ্নিত করেছি। কিন্তু এসিডের বেলায় দ্রবণীয়তা বা হাইড্রোজেন মূলক থাকার ভিত্তিতে আমরা আলাদা শ্রেণিকরণ করিনি।
এর কারণ হলো ব্রনস্টেড-লাউরী সংজ্ঞা অনুসারে এসিড হতে তাতে অবশ্যই হাইড্রোজেন আয়ন থাকতে হবে। কিন্তু বিপরীতে ক্ষার হওয়ার জন্য হাইড্রোক্সাইড মূলক থাকা আবশ্যক নয়। এছাড়া অনেক ক্ষারক পানিতে দ্রবণীয় হয় না। তাই পানিতে দ্রবণীয় ক্ষারগুলো আলাদাভাবে গুরুত্ব পায়। এসিডের বেলায় কিছু এসিড পানিতে অদ্রবণীয় হলেও অধিক ব্যবহৃত প্রায় সব এসিড পানিতে দ্রবণীয় হয়ে থাকে। তাই ক্ষারকের মধ্যে ক্ষারকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যতটা সুবিধা দেয়, এসিডের ক্ষেত্রে এমনটা নয়।